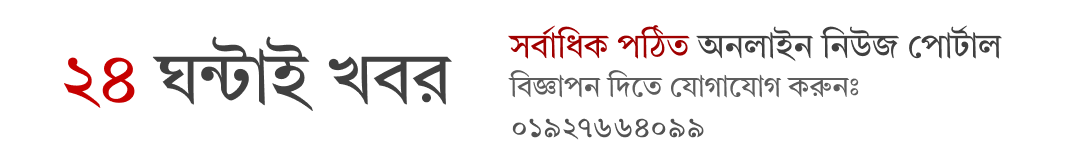বৃহস্পতিবার, ০৫ মার্চ ২০২৬, ০৯:১৯ পূর্বাহ্ন
বাবার ঘড়ি ও লুপ্ত পেন্ডুলাম

আমার ছয় ঘণ্টা ঘুমেই চলে যায়। আগে প্রথম রাতে জাগতাম। এখন শেষরাতে। উঠে চা করি, ল্যাপটপ নিয়ে বসি। শুরুতে ফেসবুকে যাই। যেন ব্যায়ামের আগের ওয়ার্ম আপ। তারপর কাজের ই-মেইলের উত্তর দিই, ভবিষ্যৎ কাজের মওকা খুঁজি। হাতে লেখা নোটগুলো জড়ো করি। তারপর লিখতে বা লেখা এডিট করতে বসি। বাইরে সুনসান বাতাস বা ঝিরঝিরে তুষার বা শীতের সুই চলতে থাকুক আর না-ই থাকুক।
কয়েক বছর আগে একরাতে লেখার জন্য জেগে দেখি, ব্লাইন্ডের ফাঁক দিয়ে আলোর চাপাতির মতো ধারালো একফালি আলো এসে পড়েছে ঘরে। সে আলো চাঁদের, না লাইটপোস্টের জানি না। বিছানা ছেড়ে উঠতে গিয়ে চমকে উঠলাম। মুখ মুছলাম বাথরুমে গিয়ে গামছা ভিজিয়ে। বিছানায় ফেরার পথে সব সময় হাত পড়ে সাদা ড্রয়ারটায়। দেখি, ওপরটা এলোমেলো হয়ে আছে। রাতে এসব গোছানোর কথা না। কিন্তু আমি তো এমনই। হঠাৎ নিচ থেকে বেরিয়ে এলো আব্বার ঘড়ির নীলচে বাক্সটা। আমার বাবার ঘড়িটা! পাশেই সেই চাপাতি।
বছর কেটে কেটে আমি এখন বিলাতবাসী। ঘড়িটা কখনো বের করিনি। কী এক আশঙ্কায়। জানি না বাবার কোনো মুখ, কোনো ভাব, কোনো স্মৃতি মনে আসবে। সে জলছাপ তাঁর টেনিস খেলে শর্টস পরে ঘরে ফেরা, নাকি সিএমএইচে রোগশয্যায় আম্মার হাতে সেবা গ্রহণরত মলিন মুখ। মানুষ চলে গেলে কেন শুধু তাঁর শেষের ছবি স্থির হয়ে থাকে। কোথায় যায় তাঁদের সেই দুর্দান্ত অশ্বারোহীকালীন মুখ! আমি তো কষ্টাক্রান্ত মুখাবয়ব মনে করতে চাই না।
বাক্সটা খুলে হাতে তুলে দেখি, ৫টায় কাঁটা স্থির হয়ে আছে। আহা রে, আমার বাংলাদেশের সেই সময়। সেই ফেবার লুভা। কালো বেল্টে এখনো আমার বাবার কবজির দাগের মাপ। প্যাসেজের অন্ধকারেই প্রবল মমতায় বাঁ হাতে সেই ঘড়িটা পরলাম। দেখি একটু ঢুলু ঢুলু করে—বালার মতো। তারপর নিজের অন্য হাতটা দিয়ে সে হাতটাকে আদর করতে থাকলাম। কাঁদতে কাঁদতে বিছানায় ফিরে এলাম।
আমার বাবা আবু আহমদ মাহমুদ তরফদার। তাঁর স্বাভাবিক প্রয়াণ হয়েছে উনষাট বছর বয়সে সেই সাতাত্তর সালের ৯ ডিসেম্বর! এখন আমিই বাবার চলে যাওয়ার বয়সের চেয়েও বয়সে অনেক বড়। কিন্তু আশ্চর্য, ডিসেম্বর এলেই আমি এক শিশু হয়ে যাই। ডিসেম্বর আমার হাহাকারের মাস। আমি কাঁদি উচ্চৈঃস্বরে। একাত্তরের পর থেকেই তা-ই হয়েছে। নিজ পিতার পরিধি ছাড়িয়ে আমার পিতৃতুল্য প্রয়াত শিক্ষকদের কথা মনে হয়।
একাত্তরের চৌদ্দ ডিসেম্বরের কথা মনে হয়। একাত্তর সালে আমার বাবা জীবিত ছিলেন। কিন্তু তখন আমার স্যারদের হত্যা করা হয়েছে। আর তাঁদের কারোরই স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি। তাঁদের দেহের অবশেষও রাখেনি বুদ্ধিজীবী হত্যাকারী খুনিরা। এখনো কানের মধ্যে বাজতে থাকে একাত্তরের ডিসেম্বরে শোনা রায়ের বাজার ঘুরে আসা অনুজপ্রতিম কিশোর মুক্তিযোদ্ধা বুলবুলের চিত্কার। তার হাহাকার এত বছর পরও আমার এই ঘরে আবারও এসে দাঁড়ায়। আমি সেই ভয়াবহ বধ্যভূমিতে জেগে উঠি।
দেখি, সেই চাপাতি ও ছুরির কোপে চোখ তোলা, আঙুল কাটা, পেছনে হাত বাঁধা আমার স্যারদের মৃতদেহ। আমার নিরীহ বাবার মতোই তাঁরাও গেঞ্জি পরতেন, ঘরে লুঙ্গি পরতেন। তাঁদের সেই সব ঘরের জামা বেয়নেটের খোঁচায় খোঁচায় ফাড়া। আহা রে, যাঁদের কেউ কোনো দিন অশ্রদ্ধা করে জোরেও কথা বলেনি, যাঁরা জীবনে কোনো দিন অস্ত্রের মুখ দেখেননি; তাঁদেরই কী তীক্ষধারালো অস্ত্রে কী কষ্ট দিয়ে কেটেছে! মাটিতে পড়ে ছিল বাংলাদেশের সূর্যসন্তানদের দলিত-লাঞ্ছিত মৃতদেহ। দেশের সবচেয়ে সম্মানিত সন্তান—তাঁদের একি হাল! এসব মহাপ্রাণের প্রতি একি সাংঘাতিক অপমান, অন্যায়! চারদিকে থান থান খয়েরি ইট আর জল। সে জল ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদের রক্ত ও ক্রন্দন।
‘মানুষ চলে গেলে তার পালক রেখে যায়। জ্ঞাতি চিহ্ন দেখে দেখে পরশ বোলায়।’ কাঁদে। আমি মাঝেমধ্যে আমার মায়ের শাড়ি ও ধানছড়া সোনার হার ছুঁয়ে দেখি। শাড়ি হাতে নিলে ঘ্রাণ নিই। এখন ঘ্রাণ নাকে আর পাই না, পাই মনে। সে গোলাপের মতো ম ম করে। সে সময় আমাদের বাবারা কোনো গয়না পরতেন না। বাবাদের কোনো সোনার গয়না থাকে না। আব্বার একটা ঘোলা চোখের মতো আকিক পাথরের রুপার আংটি ছিল। তাঁদের কোনো মোবাইল ছিল না যে সময় দেখবেন। আমাদের বাবারা মণিবন্ধে ঘড়ি পরতেন।
দুই.
আমার স্যার শহীদ অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর কবজিতেও ওরকমই একটা লালচে খয়েরি বেল্টের ঘড়ি ছিল। তিনি পরতেন ঘিরঙা খদ্দর বা দেশি সুতির লম্বা পাঞ্জাবি। তাঁর পায়জামা সাদা আর ঘেরওয়ালা। শু পরা দেখেছি কি? মনে পড়ে না। তাঁর ছিল বেল্টওয়ালা স্যান্ডেল। চশমার ফ্রেম মোটেও ‘ওয়ার অ্যান্ড পিসের’ পিটারের (স্যার বলতেন পিয়ের) মতো ছিল না। তাঁর চশমা ছিল ভারী আর মোটা। এই এখন যা আবার সিক্সটিজ বলে ফিরে এসেছে। তবে তাঁর ভেতরে ছিল বিদ্ধ হওয়ার মতো দৃষ্টি।
সে চোখ মাছের শীতল স্লিপারি করিডর মেঘের মতো ঢেকে দিত। আবার বাংলা বিভাগ প্রধানের কক্ষে তাঁর সামনে গেলে মনে হতো, সেই চোখ জোড়াই সকালের সূর্যের মতো আমার গায়ে রেণু গজাচ্ছে। আবার চোখ জোড়াই ক্লাসরুমে শরত্চন্দ্রের নির্বোধ শ্রীকান্ত, শেকসপিয়ারের ম্যাকবেথের এক শব্দে দুই অর্থ করা প্রেতিনী কিংবা তলস্তয়ের পয়মাল পিটারের চোখ হয়ে যেত। অবাক হয়ে দেখতাম, কী করে তিনি নানা প্রযত্নে নানা মানুষ হয়ে যান। একি অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। শুধু তা-ই নয়, বিকেলে সেমিনাররুমে রিহার্সালে তিনি হয়ে যেতেন হাইকোর্টের বিচারক। উচ্চারণের অবহেলা তাঁর কাছে অসহ্য ছিল। এ নিয়ে অবশ্য সব শিক্ষকই সমান নির্মম ছিলেন। সন্ধ্যায় টিএসসিতে নাটক চলাকালে অন্ধকারে পেছনের সিটে বসা স্যার আমাদের একগুচ্ছ স্বেচ্ছাসেবকের কাছে হয়ে যেতেন বাৎসল্যে গলে যাওয়া বৈদূর্যমণি।
কখনো কখনো স্যার সাইকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতেন। ঢোলা পায়জামা বা ট্রাউজার ভাঁজ করে বেড়ি আটকে। তখন উনসত্তরে সাইকেলস্ট্যান্ড ছিল কি না, মনে নেই। কিন্তু স্যারের সাইকেল সরাসরি বাংলা বিভাগের নিচে কলাভবনের সামনে নিচতলার করিডরের কংক্রিটের সাদা দেয়ালে হেলান দিয়ে শুকনো ঘাসে দাঁড়িয়ে থাকত। হয়তো চৌর্যবৃত্তি ঠেকানোর জন্য। ডান হাতলের পাশে ছোট্ট ওল্টানো রুপালি বাটির মতো বেল। তার আগে সামনের চাকার ওপর হাতলের মধ্যভাগে আটকানো বেতের বাস্কেটে বই। হয়তো লাইব্রেরির। হয়তো তাঁর নিজের। তাই তিনি যখন অন্য ক্লাসে, তখন বাংলা বিভাগের সামনের কংক্রিট দেয়ালে নদীর মতো হেলান দিয়ে নিচে তাঁর সাইকেলের বাস্কেটের বইগুলোর শিরোনাম পড়ার চেষ্টা করতাম।
তিন.
আমার স্যার মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী পড়াতেন রবীন্দ্রনাথের কবিতা। শান্তিনিকেতনের প্রথম শ্রেণি পাওয়া ছাত্র—এত মেধাবী, এত গুণের আকড়, এ তো এক বিশ্বকোষ। শান্তিনিকেতনে তাঁকে বলা হতো ‘মুখোজ্জ্বল চৌধুরী’। যেকোনো বেলায় দেখলেই মনে হতো, যেন সদ্য শীতল জলে স্নান করে এসেছেন। তিনি পরতেন পায়জামা-পাঞ্জাবি ও কালো ওয়েস্ট কোট। পায়ে বেল্ট দিয়ে আটকানো স্যান্ডেল। কিন্তু কথা বলতেন এত নরম করে, যেন বাতাসের গায়ে আঁক বসে বাতাস ব্যথা না পায়। ক্লাস নিতেন, যেন তিনি বসে আছেন নিজের ঘরের মেহগনি কাঠের এক হাতাওয়ালা চেয়ারে। আর আমরা তক্তপোশে।
স্যার সবলা পড়তে ও পড়াতে পড়াতে গল্প করতেন শান্তিনিকেতনের মেয়েদের কথায়। যেখানে ইন্দিরা গান্ধীও একজন সাধারণ মেয়ের মতো খালি পায়ে এক বাক্স কাপড়চোপড়ে দীক্ষা নিয়েছেন। ছাতিমতলার গাছের ছায়ায় সংগীতের মায়ায় নিজেকেও করে তুলেছিলেন তেমনি সাদাসিধে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাম দিয়েছিলেন ‘প্রিয়দর্শিনী’।
বলাকা পড়াতে পড়াতে স্যার যখন বলতেন, সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের শ্রোতখানি বাঁকা/আঁধারে মলিন হলো যেন খাপে ঢাকা বাঁকা তলোয়ার। আর বাণী ভেঙে কবিতার বল বের করে আনতেন, আমার মনে হতো কপ করে ধূসর ধাতবের খোপে সাঁই করে সেঁটে গেল রুপালি পারদ। চোখ ও মগজ আটকে যেত স্যারদের কথায়। ক্লাসের সময় দুম করে শেষ হয়ে যেত।
স্যারদের কোনো মোবাইল ছিল না যে সময় দেখবেন। আমাদের পিতারা মণিবন্ধে ঘড়ি পরতেন।
স্যার গল্প করতেন শান্তিনিকেতনের একেকটি বাড়ির কবিতার মতো নাম নিয়ে। শুদ্ধ উচ্চারণে কবিতা পাঠ করতে না পারলেও, প্রশ্নের উত্তর সঠিক না দিলেও, বকাটা দিতেন নরম করেই। আমরা বলতাম, শান্তিনিকেতন তাঁর মাথায় একটি ফ্রিজ ঢুকিয়ে দিয়েছে। সন্দেহ হয়, স্যার জীবনে কাউকে হালকা চড়চাপড়ও দিয়েছেন কি না।
তখন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমরা অসহযোগ আন্দোলন করছি। পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে দানা বেঁধে উঠছে আমাদের সংগ্রামী মন। করিডরে করিডরে ব্যাপক দৌড়াদৌড়ি আর স্লোগান। বটতলায় লাগাতার মিটিং। তাঁর কক্ষের সামনে দিয়ে ছুটে যাচ্ছিলাম। একটু কৌতুকময় মৃদু হাস্যে বললেন, তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে আসব। আমাদের সোবানবাগের বাসার ঠিকানা লিখে নিলেন।
তারিখ ঠিক হলে আমি আর আব্বা বিকেলে দোতলার ব্যালকনিতে অপেক্ষায় ছিলাম। স্যার দেখি, তাঁর ছোট্ট গাড়িটি ফ্ল্যাটের সামনে পার্ক করে কোমরে লেদার বেল্ট ও জিন্স পরা মনসুর মূসা স্যারসহ বেরিয়ে আসছেন। আমি তো উত্তেজনায় বাঁচি না। আম্মা খয়েরি করে ঘিয়ে ভেজে সুজির হালুয়া করেছেন। চা ও হালুয়া ট্রেতে ওঠাতে ওঠাতে কান পেতে অবাক হয়ে যাই। তাঁর প্রিয় ছাত্রীটির জন্য সে সময়ের উজ্জ্বলতম মেধাবী ও সর্বদা সত্যভাষী এক তরুণ শিক্ষকের জন্য বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন। আব্বা তো মহা আহ্লাদিত! তাঁর কন্যার কারণে এমন সব নমস্য মানুষের আগমন ঘটেছে আমাদের ঘরে! ততক্ষণে আম্মাও সে ঘরে গেছেন। প্যাসেজ থেকে তাঁদের মিলিত হাস্য-কথন শুনে মনে হলো, যেন মা-বাবার বন্ধুরা এসেছেন। স্যারের মণিবন্ধের ঘড়িটি গোলাকার, না চৌকা ছিল মনে নেই। তবে বন্ধনীটা ধাতব ছিল না। রুচিবানরা সেসব পরিহারই করতেন।
চার.
আমার স্যার আনোয়ার পাশা পড়াতেন রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ। স্যার অনেক দ্রুত কথকতায় কাদম্বিনী, চারুলতা, নরেশ, ভূপতি, রতন—সবাইকে এনে ক্লাসরুমে দাঁড় করিয়ে ফেলতে পারঙ্গম ছিলেন। স্যারের নিজের গদ্যের হাত ছিল শক্তিজলে ধোয়া। ছোটগল্পই একা শিল্পকর্ম হিসেবে যে একটা মহাকারুকার্যময় ব্যাপার, ওই ব্যাপারের আগে যে শ্যাপারগুলোও পড়তে হয়, আর তার জন্য যে পাবলিক লাইব্রেরি ও বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরির সামনে স্যান্ডেল ক্ষয় করতে হয়, স্যারের ক্লাসেই তা প্রথম মনে হলো।
লিখেছিলেন সেই বিখ্যাত উপন্যাস—‘রাইফেল, রোটি, আওরাত’। পড়েছি কি না মনে নেই। কিন্তু নামটা শুনলেই কি মনে হয় না, এ এক অশনিসংকেত, যা বাংলাদেশে হতে যাচ্ছে? স্যার কি তবে এক সন্ত পুরুষ ছিলেন, যিনি ভবিষ্যৎ দেখতে পারতেন? কিন্তু নিজের নির্মম ভবিষ্যৎ তো দেখতে পাননি এ ভবিষ্যত্দ্রষ্টা? নিজের ভবিষ্যেক সুরক্ষা করতে ভেবেছিলেন, পাকিস্তানই তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্য। ভারত থেকে তাই শরণার্থী হিসেবে এ দেশে এসেছিলেন স্যার। যে দেশকে নিরাপদ ভেবেছিলেন, সেখানেই তাঁকে প্রাণ দিতে হলো!
নাতিদীর্ঘ মানুষ ছিলেন স্যার। বুকের কাছে ধরা ছোটগল্পের মহামোটা এক ডিকশনারি মার্কা বই। যেন তাঁর দেহের অংশ। যেন তাঁকে ছাড়েনি কখনো। ছাড়ে না কিছুতেই। হাঁটতেন ক্ষিপ্র পায়ে। কথা বলতেন দ্রুত। করিডর দিয়ে হেঁটে গেলে ‘পিছু নিচ্ছি নেব’ করলেই আর স্যারকে পাওয়া যায় না। স্যারের চোখে ঠিক আমার বাবার চশমার মতো কালো মোটা প্লাস্টিক ফ্রেমের চশমা ছিল। তাতে আয়তক্ষেত্রের আকার ছিল। কবজিতে ছিল সে সময়ের বাবাদের মতো ঘড়ি।
পাঁচ.
আমার কান্না কখন যেন শুকিয়ে গেছে। টেবিললাইট জ্বালাতেই সেই চাপাতি লাফিয়ে মিলিয়ে গেছে। আমার হাতে পড়ে থাকে আমার বাবার সেই স্তব্ধ ঘড়ি। আমি কুঁকড়ে বিছানায় পড়ে থেকে বাংলাদেশের দেহঘড়ির ভেতরের স্বর্ণাভ পেন্ডুলাম যারা স্তব্ধ করে দিয়েছে, তাদের তীব্র অভিসম্পাৎ করি। তখন আরেক কান্না গাছের মতো গজায় আর আমার সারা দেহে হাজার হাহাকার তোলে। সেই আর্তিতে আমার জন্মদাতা পিতা ও অভিজ্ঞানদাতা পিতারা এক এবং একাকার হয়ে যান।
লেখক : শামীম আজাদ