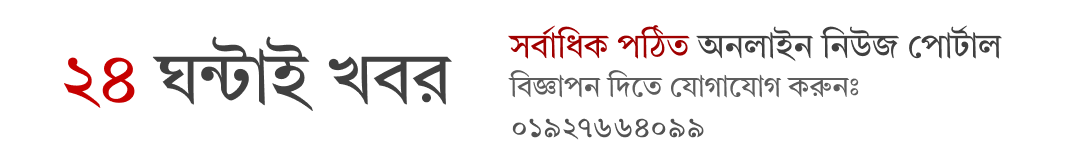সোমবার, ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০৯:২০ অপরাহ্ন
প্রচার বিমুখ একজন ভাস্কর্য শিল্পী চিত্ত হালদার’এর প্রয়াণ দিবস

ভায়লেট হালদার: আমার বাবা Chitta Halder (১৯৩৬-১৯৭৮)। আজ তার ৪২তম প্রয়াণ দিবস। মানুষের কাছে আজ বিস্মৃত তিনি; তিনি বাংলাদেশের তার সময়ের একজন প্রথিতযশা ভাস্কর্যশিল্পী ও চিত্রশিল্পী ছিলেন। বাবা প্রয়াত হয়েছেন বিয়াল্লিশ বছর আগে। এই বিয়াল্লিশ বছর বাবাকে ছাড়া বড় হলাম, শীতের রুক্ষ পাতাহীন বৃক্ষের মতো। আমার মা ঝর্ণা হালদারের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ জীবনযুদ্ধের একক সংগ্রামের সঙ্গে আমরা তিন বোন ক্ষুদে তিন সৈন্য ছিলাম। বাবা যখন মারা গেলেন, বড় বোন জুলিয়েট হালদার তখন মোটামুটি বড়, আমি মেঝ আর ছোট ব্রিজেট হালদার ছিল মাত্র দেড় বছর বয়সী। আমি ও বড় বোন বাবার স্নেহ-আদর কিছুটা হলেও পেয়েছি; কিন্তু আমার ছোট বোন বাবার স্নেহ-আদর থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ছোট বোনের ‘বাবা’ ডাকটি ডাকার আগেই প্রকৃতির নিষ্ঠুর নিয়মের কাছে পরাজিত হয়ে বাবা চলে গেছেন। শুধু রেখে গেছেন তার স্মৃতি, শিল্পকর্মগুলো আর আমাদেরকে। বাবাকে নিজের ভেতর গভীরভাবে জানা ও উপলব্ধি করার আগেই তিনি চলে গেছেন। আমাদের উপলব্ধির খাতা অপূর্ণই থেকে গেল। আমার পিসীমা প্রেমলতা হালদার, মাসীমা ইন্দিরা হালদার, মা, বড় বোন এবং আমাদের নিকটতম শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছ থেকে বাবার মাত্র ৪২ বছরের জীবনের কথাগুলো শুনে শুনেই বাবাকে জেনেছি, বুঝতে শিখেছি, ভালবেসেছি।
বরিশালের গোঁড়াচাঁদ দাস রোডে কাটে তার আজীবন। পিসীমার কাছে শুনেছি, চিত্রকলায় ও ভাস্কর্যশিল্পে বাবার কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না। বাবা শিশুকাল থেকেই ছবি আঁকতেন। সেসময়, চল্লিশের দশকের প্রথম দিকের কথা, তার পোষা কুকুরের নাম ছিল হান্টার। হান্টার ছিল ভীষণ তেজস্বী। একদিন তিনি হান্টারের লেজ থেকে কিছু পশম কেটে গাছের ডাল কেটে তুলি বানান। বিভিন্ন গাছ থেকে ফল সংগ্রহ করে রঙ বের করে তখন ছবি আঁকার কৌশল নিজে থেকে আয়ত্ত করেছিলেন। এমনকি আঁকার কাজে তিনি তখন কাঠকয়লা, বোনেদের আলতা ব্যবহার করেছেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি একটু একাকী নিজস্ব শিল্পের জগতে ডুবে থাকতে পছন্দ করতেন। কখনো নিজ হাতে রঙবেরঙের ঘুড়ি ও নাটাই বানাতেন ও ঘুড়ি ওড়াতেন। সে কারণে তিনি তার বন্ধুমহলে শিশুবেলায় বেশ জনপ্রিয় ছিলেন। স্কুলজীবনে তিনি ধুতি পড়তেন, নয়-দশ বছর বয়স পর্যন্ত তার ধুতি পড়তেন বলে শুনেছি। বাড়ির সামনে খালে তিনি স্নান করতেন। পড়াশুনার পেছনে খুব বেশি সময় ব্যয় করতেন না বলে আমার ঠাকুরদা বিশ্বনাথ হালদার শাস্তি হিসেবে প্রায়ই ভাত খাওয়া বন্ধ করে দিতেন। কিন্তু পিসিমা আর ঠাকুরমা তরী হালদার দু‘জনে লুকিয়ে লুকিয়ে বাবাকে খাওয়াতেন। কখনো খেলায় ও ছবি আঁকায় মগ্ন থাকতেন যে তার বিদ্যালয়ে যেতে দেরী হয়ে যেত, তখন তার মা তাকে ধরে এনে খাইয়ে-দাইয়ে স্কুলে পাঠাতেন। এমনও হয়েছে যে বাবা হয়তো কোন একদিন স্কুলের দেয়া পড়া পড়েননি, তিনি স্কুলের যাওয়ার পথে নিজের সিলেটে কিংবা রাস্তার পাশের দেয়ালে চক দিয়ে সে অঙ্ক করতে করতে যেতেন। তার বিদ্যালয় জীবন শুরু হয়েছিল বগুড়া রোডে অক্সফোর্ড মিশন পাঠাশালায়, এরপরে বরিশাল জিলা স্কুল ও পরে বরিশাল বি.এ. স্কুল (ব্রজমোহন বিদ্যালয়) থেকে তখনকার মেট্রিকুলেশান পাস করেন। এরপরে তার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা জীবন সম্পর্কে আর জানা যায়নি। তিনি বরিশাল জিলা স্কুলে ক্লাশ ফাইভে পড়াকালীন সময়ে সরকারী শিক্ষা বৃত্তি পান, তা নিয়ে তার বাবা গর্ব করতেন। বৃত্তির মূল্যমান ছিল সেসময়ের ২৫ পয়সা, তার পুত্র বৃত্তি পাওয়ার কারণে এলাকার মানুষ তাকে সম্মানের চোখে দেখতো।
পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি সময়ে বরিশাল শহরের কালিবাড়ি রোডে বাবা ‘চিত্রালি’ নামে বাণিজ্যিক ছবি আঁকার একটি দোকান খুলেছিলেন। প্রথম দিকে সেখানে তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ড, শ্বেতপাথরের নামফলক, ব্যক্তির পোট্রেট প্রভৃতির কাজ অর্থের বিনিময়ে করতেন। পরে তিনি সে কাজ ছেড়ে দেন। বাঁশ, মাটি, পাথর, প্লাস্টার অব প্যারিস ইত্যাদি উপাদান থেকে ভাস্কর্য বানাতেন। তার তৈরি এ সমস্ত হস্তশিল্পগুলো ঢাকার স্বনামধন্য বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে যেমন ‘বাংলাদেশ এজেন্সী’, ‘মলজ’, ‘ভোগ’, ‘তৈজস’, ‘শীষমহল’ থেকে দেশী-বিদেশীদের কাছে বিক্রি হয়েছে এবং প্রশংসা পেয়েছে। তিনি ১৯৫৯ সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন, বরিশালের ব্যাপ্টিস্ট মিশন রোডে ব্যাপ্টিস্ট চার্চে তার বিয়েতে দু’পরিবারের আত্মীয়স্বজনরা ছাড়াও তার কাছের বন্ধুরা যারা এসেছিলেন তাদের মাঝে অন্যতম ছিলেন ডাঃ রণজিৎ কুমার বড়াল ও পরবর্তী সময়ের চলচ্চিত্র পরিচালক পুলিন মিত্র। স্বাধীনতার পরে পুলিন মিত্র একজন সহকারী চলচ্চিত্র পরিচালক ও অভিনেতা হিসেবে ‘জিঞ্জির’ চলচ্চিত্রে কাজ করেন। বিয়েতে দিলীপ বিশ্বাসও এসেছিলেন, দিলীপ বিশ্বাস (১৯৪৬-২০০৬) পরে বাংলাদেশের সিনেমার প্লেব্যাক গায়ক, চলচ্চিত্র প্রযোজক ও খ্যাতিমান চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠেন। বরিশাল শেরে বাংলা মেডিক্যাল কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর ১৯৬৪ সালে স্থাপিত হয়, সে সময়ে সে ভিত্তি প্রস্তরস্তম্ভটি বাবা ইংরেজীতে খোদাই করে দিয়েছিলেন।
১৯৬৫/৬৬ সালে তিনি একটি বক্স ক্যামেরা ও ফটো এনলারজার বানিয়েছিলেন, যা দিয়ে আমাদের পুরনো দেয়ালসেট টিনের ঘরের অন্ধকার একটি রুমে ফটো তুলে প্রিন্ট করতেন। তিনি নিজ হাতে ব্লেজার, হাতের চুড়ি বানিয়ে আমার মা’কে পরিয়েছেন। কিছু আসবাবপত্র খাবার টেবিল, স্যুটকেস নিজ হাতে বানিয়েছেন। মাঝেমধ্যে রান্না করতেন। আমার মাসীমা’র কাছে শুনেছি তিনি নিজ প্রয়োজনে গিটার, বেহালা বানিয়েছেন। কিনেছিলেন তানপুরা। বাজাতে পারতেন বাঁশি, গিটার, বেহালা, তানপুরা। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে নিহত শহীদদের স্মরণে কালিবাড়ি রোডে বর্তমান জগদীশ গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের সামনে বাবা নির্মাণ করেন শহীদ মিনার মিনার, যা এখনও অনাদরে-অবহেলায় হলেও কালের সাক্ষী হয়ে টিকে আছে। বরিশালের ভাষা আন্দোলনের সৈনিক রাণী ভট্টাচার্য যিনি এক সময় জগদীশ গার্লস স্কুলের শিক্ষক ছিলেন, ওনাকে আমরা পিসীমা বলে ডাকতাম, তিনি বাবাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। নব্বই দশকের মাঝামাঝি নারীদের অধিকারভিত্তিক সংগঠন বরিশাল মহিলা পরিষদের সাথে আমার সম্পৃক্ততা থাকার কারণে রাণী পিসিমার কাছে থেকে বাবার অনেক স্মৃতিময় কথা শুনেছি। এই রাণী পিসিমাই বাবাকে ডেকে এনে এই শহীদ মিনারটি তৈরি করিয়েছিলেন।
১৯৭১ সালে সারা দেশ জুড়ে স্বাধীনতা যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। যদিও তখনও বরিশাল শহরে পাকিস্তানী সেনারা এসে পৌছায়নি। গোঁড়াচাঁদ দাস রোডে আমাদের বাড়ির পাশে সাহেবের কবরস্থানের ভেতরে একটি বহু পুরান কবর খোঁড়া হয়েছিল লুকিয়ে থাকার জন্য। কবরটির বয়স এখন হবে অন্তত দুইশ’ বছরের বেশি। বাবা তার কয়েকজন ছোটভাইসম বন্ধুদের নিয়ে বসলেন, কেমন করে পাকিস্তানী সেনাদের রুখে দেওয়া যায়। অস্ত্র সঙ্কটের কথা ভেবে তিনি হাত বোমা, মলোটভ ককটেল বানানোতে উদ্যোগী হন। কিন্তু তিনি কখন কবে এ বিদ্যা রপ্ত করেছিলেন তা সম্পর্কে নির্দিষ্ট তথ্য তিনি প্রকাশ করেননি। তবে ধারণা করা হয় এক সময়ে বরিশালের বিট্রিশ বিরোধী আন্দোলনকারীদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল, হয়তো সেখান থেকে তিনি বোমা বানানো শিখেছিলেন। এক রোববারে বাসার সকলে গিয়েছিল ফজলুল হক এভিনিউতে উদয়ন স্কুলের সামনের গীর্জায় (বর্তমানে চার্চ অব বাংলাদেশ)। বাড়ির সকলে ফিরে দেখে যে বাবা বোমা নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে দু’পায়ে কিছুটা আহত হয় শুয়ে শুয়ে নিজেকে বাতাস করছেন। এরপর ডাক এলো প্রগতিশীল তরুণদের সাংস্কৃতিক সংগঠন ‘বরিশাল যুব সংঘ’ থেকে। সেখানে তার সঙ্গে আরো কিছু যুবক একত্রিত হলেন, সেই কালিবাড়ি রোডে ‘ধর্মরক্ষিণী সভা’ নামক হিন্দুদের মিলনস্থানটি উন্মুক্ত হলো বরিশাল যুব সংঘের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য। বাবা হাতে অন্যান্যদের সহযোগিতায় তৈরি হতে থাকলো একের পর এক বোমা। মেজর জলিল এলেন, বাবাকে তিনি স্থানীয় উপাদানে তৈরি স্বল্পমাত্রার রকেট লাঞ্চার, ডিনামাইট ও বোমা বানাতে বললেন। বাবার তৈরি এসব বোমা পরবর্তীতে চাঁদপুর, খুলনার গল্লামারী যুদ্ধে সাফল্য এনে দেয় বলে জানা গেছে। বোমা তৈরির কাজে তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সহযোগী ছিলেন হেলাল উদ্দিন, ওয়াহিদুজ্জামান কচি, এনায়েত হোসেন মিলন (প্রয়াত), বাকীরা বোমা বহন কাজে নিযুক্ত ছিলেন।
১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল একজন পাক গুপ্তচর ধরা পড়ে। মেজর জলিল (পরবর্তীতে ৯নং সেক্টর কমাণ্ডার) তাকে বেলসপার্কে নিজে গুলি করে মেরে ফেলেন। এরপরে ২৫ এপ্রিল সড়ক ও নৌপথে আক্রমণ এবং জেটবিমান থেকে শেল নিক্ষেপ করার পরে ছত্রীসেনা নামিয়ে বরিশাল শহর দখল করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। বাবার বানানো একটি বোমা দিয়ে বরিশাল রহমতপুরের ব্রীজ উড়িয়ে দেওয়া হয় এবং তখন পাক সেনাদের কয়েকটি গাড়ি বিধ্বস্ত হয় ও কিছু পাক সেনা সেখানেই নিহত হয়। এরপরেই পাক আর্মির ব্লাক লিস্ট তালিকায় বাবার নাম যুক্ত হলো। বাবাকে খুঁজতে স্থানীয় রাজাকাররা ও পাক সেনারা ঘন ঘন আমাদের বাসায় বাবার খোঁজে আসতে শুরু করে। আমার ঠাকুর্দা উর্দু জানতেন বিধায় পাক সেনাদের সঙ্গে তিনি উর্দুতে কথা বলতেন। হিটলিস্টে নাম অন্তর্ভূক্ত হওয়ার কথা গোপনসূত্রে জানতে পেরে তিনি স্বপরিবারে বরিশাল ত্যাগ করে বরিশাল যুবসংঘের তৎকালীন সভাপতি এস.এম. ইকবালের বানারীপাড়ার বাড়িতে, উজিরপুরের ধামসরে আমার ঠাকুর্দার পৈতৃক বাড়ি ও কালনাগা গ্রামে আমার এক নিকটাত্মীয়ের বাড়ি, আগৈলঝাড়া উপজেলার জোবারপাড় গ্রামে অন্য এক আত্মীয়ের বাড়ি পালিয়ে থাকেন; কিন্তু সেখানেও থাকা অনিরাপদ হয়ে ওঠে। সেখানে ডাকাতের কবলে পড়েন। তারপর সেখান থেকে নৌকাযোগে চলে যান গোপালগঞ্জ জেলার আমার আপন পিসিমা প্রেমলতা হালদারের বাড়িতে, খাকবাড়ি গ্রামে। কিন্তু সেখানেও তার খোঁজে লোক গেলে তিনি স্বপরিবারে দেশ ছাড়তে বাধ্য হন। বিভিন্ন পরিচিত-অপরিচিত মুক্তিযোদ্ধারা তাকে সহায়তা করেন। আমার পরিবার মূলত হেঁটে বনগাঁ হয়ে শরণার্থী হিসেবে ভারত যায়। দিনের বেলা রাস্তার পাশে জঙ্গলে সকলে লুকিয়ে থাকত, আর রাতের বেলা পথ চলত। তবু পথে পাক সেনারা পথ আটকিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে,কিন্তু বাবার পরিচয় জানতে পারেনি। নৌকায় একবার নদী পার হওয়ার সময় আগের নৌকায় বরিশালের এক সুপরিচিত ব্যক্তির মেয়েকে রাজাকাররা ধর্ষণ করে। তাদের সঙ্গে দেশত্যাগীদের দলে চিত্রশিল্পী হাসি চক্রবর্তীর পরিবারও ছিল। পরে বাবা স্বপরিবারে কলকাতার দমদমে তার কাকাত ভাই নিরঞ্জন করের বাড়িতে ওঠেন। বরিশালের বাসায় তখন আমার ঠাকুর্মা, ঠাকুর্দা ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। বাবাকে না পেয়ে আমার ঠাকুর্দাকে অন্তত দু’বার পাক সেনারা ধরে নিয়ে যায়, বাবার অবস্থান জানার চেষ্টা করে অল্পস্বল্প টর্চার করতো, দু’তিন দিন পরে ছেড়ে দেয়। সেসময় আমার ঠাকুর্মার গরু জোর করে পাকি রাজাকারেরা নিয়ে যায়। সে গরু দড়ি ছিঁড়ে চলে আসে।
বরিশাল মুক্ত হয় ৮ ডিসেম্বর। তিনি খবর পেয়ে দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন। ১৬ ডিসেম্বর বরিশাল এসে পৌঁছান। বাবা ফিরে এসে দেখেন বাবার বানানো সব বাদ্যযন্ত্র, চিত্রকর্ম, ভাস্কর্য, মূল্যবান বইপত্র, পিতলের দাড়িপাল্লা, কাঁসার তৈজসপত্র, তিনটি ক্যামেরা, দূরবীন, ঘড়ি, ছবি ছাপার মেশিন দোকান ও বাসা থেকে লুট হয়ে গেছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে অর্থনৈতিক অবস্থা খুব খারাপ, তিনি ঠিক করলেন যে তিনি আর বরিশালে কাজ করবেন না। যৎসামান্য অর্থ নিয়ে ১৯৭২ সালে তিনি রাজধানী ঢাকায় চলে যান। ঢাকার ফার্মগেটের কাছে রাজাবাজারে তিনি দুই রুমের একটি বাসা ভাড়া নেন এবং সেখানে ব্যক্তিগতভাবে তার শিল্পকর্মের কাজ চালিয়ে যান ও জীবন নির্বাহ করেন। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী পটুয়া কামরুল হাসান তাকে পরিচয় করিয়ে দেন সেসময়ে নিমতলীতে অবস্থিত ঢাকা জাদুঘরের তৎকালীন পরিচালক ড. এনামুল হকের সঙ্গে, তিনি পরবর্তীতে শাহবাগে স্থানান্তর্তি জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক নিযুক্ত হন। তৎকালীন ঢাকা জাদুঘরে সংরক্ষিত হিন্দুধর্মের দেবী ‘মহামায়া’র একশত রেপ্লিকা তৈরি করে দেন। পরে সেগুলো জাদুঘর থেকে দেশী ও বিদেশী সংরক্ষকদের কাছে বিক্রি করা হয়েছিল। পুরনো নথিপত্র ছাড়াও বাবাকে নিয়ে নির্মিতব্য তথ্যচিত্র নির্মাণের কাজে গিয়ে এ কথা ড. এনামুল হকের থেকেও জেনেছি। তার কথানুসারে, মুক্তিযুদ্ধের পরে জাদুঘরকে আকর্ষণীয় করার জন্য বাবার অবদান স্বীকার করে তাকে চাকুরী দিতে চেয়েছিলেন তৎকালীন পরিচালক ড. এনামুল হক। কিন্তু বাবা চাকুরীর নিয়ম-শৃঙ্খলের নিগড়ে নিজেকে বন্দী করতে চাননি, তিনি সে প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। আমৃত্যু তিনি শিল্পীর স্বাধীন শিল্প জীবন কাটিয়েছেন। অঢেল অর্থ-বিত্ত রেখে যাননি; কিন্তু অফুরন্ত সুনাম রেখে গেছেন।
আমার দেখায় আমার বাবা ছিলেন অত্যন্ত গুরুগম্ভীর মানুষ। কাছে না ডাকলে নিজে থেকে বাবার কাছে যাওয়া হতো না। বড় বোনও যে খুব একটা বাবার কাছে ঘেঁষতেন তাও স্মরণ করতে পারছি না। দূর থেকেই আমরা দেখতাম। আমরা পরিবারের সবাই বরিশালেই থাকতাম, প্রতি মাসেই বাবা বরিশাল আসতেন আর আমরাও মাঝে মাঝে ঢাকায় যেতাম। বাবা বাড়িতে থাকলে মা আমাদের চা পান করতে দিতেন না, কেননা তিনি চা পান করা পছন্দ করতেন না। তিনি চুরুট খেতেন। বাবা কখনো ঢাকায় বসে সকালবেলা আমাদের জন্য খাবার রান্না করে সন্ধ্যার মধ্যে রকেটে চড়ে নিয়ে আসতেন। বাড়িতে থাকলে কখনো কাস্টার্ড বানাতেন, বরিশালেও আমাদের জন্য মাঝেমধ্যে নিজ হাতে রান্নাও করতেন। একবার ঢাকায় গিয়ে দেখি তিনি বিস্কুট বানিয়ে রেখেছেন। রোজ নিয়ম করে বিকেলবেলার নাস্তায় তার হাতে বানানো বিস্কুট খেতে পেতাম।
বাবার সঙ্গে আমার শেষ স্মৃতি ১৯৭৬/১৯৭৭ সালে বরিশালের এক্সিবিশনে যাওয়া। তখনকার বরিশালে স্টেডিয়ামে প্যাণ্ডেল তৈরি করে মানুষের বিনোদনের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রদর্শনী হত। যেমন: সার্কাস, পুতুল নাচ, হাউজি ও বিভিন্ন পণ্যের দোকান। বরিশালবাসী একে ‘এক্সিবিশন’ বলত, এবং সারা বছর অপেক্ষা করে থাকতো। সে এক্সিবিশন থেকে রাতের বেলা মাইক থেকে ভেসে আসতো গান। কেমন যেন একটা উৎসবের আমেজ জুড়ে থাকতো চারদিকে, মনের ভেতর আনন্দ অনুভব করতাম। সেই শেষবার আমাদের নিয়ে বাবা এক্সিবিশনে গেলেন। কিনে দিয়েছিলেন ‘বাক বাকুম জামা’, যদি ‘বাক বাকুম জামা’ বলে কিছু আছে কি না জানি না। ‘ড্যান্সিং ফ্রক’ নামে পরিচিত জামাকে আমি নাম দিয়েছিলাম ‘বাক বাকুম জামা’। বাবার কাছে সব সময় এ একটাই আবদার আমার থাকতো, বাক বাকুম জামা লাগবে। এক্সিবিশন থেকে বাবা আমাকে কিনে দিয়েছিলেন হালকা বেগুনী রঙের মধ্যে গোলাপ ফুলের প্রিন্ট করা, কোমরে কুচি দেওয়া সে জামা আর একটি লাল রঙের প্লাস্টিকের কলস।
১৯৭৭ সালের বাবার সঙ্গে কাটানো শেষ বড়দিনে তার দেয়া উপহার হিসেবে পেয়েছিলাম কালো ও লাল রঙের উলের সোয়েটার। সেই সোয়েটারের ভাগ পরবর্তীতে আমার ছোট বোন ব্রিজেট, বড় বোনের ছেলে মাইকেঞ্জেলো ও আমার মেয়ে ভার্জিনিয়া পেয়েছে। বাবার বইয়ের ভাল সংগ্রহ ছিল। দু‘টো বুকসেলফে সেসব বই থাকতো। বেশি ছিল ইংরেজি ভাষায় লেখা। বইগুলো ছিল বিভিন্ন সময়কালের দেশী-বিদেশী চিত্রকলা, দর্শন ও সাহিত্যের উপর। ইংরেজি গ্রন্থগুলোর মধ্যে শেক্সপীয়ার, নীটশে, কীটস, ওমর খৈয়াম প্রমুখদের গ্রন্থ ছিল। বাংলা গ্রন্থগুলোর মধ্যে শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, বিখ্যাত গোয়েন্দা চরিত্র ‘কিরিটি’র জনক নীহাররঞ্জন গুপ্ত প্রমুখের গ্রন্থের কথা আজ মনে পড়ে। এসব গ্রন্থ স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে লুট হবার পরেও এসব গ্রন্থগুলো অবশিষ্ট ছিল। তার মৃত্যুর পরে এসব আমার গ্রন্থ পড়ার সুযোগ হয়েছিল। বাবার বানানো লাটাই ছিল আমাদের ঘরে, সেটার অনেক ওজন ছিল যা আমার ছোটবেলায় ঐ লাটাইটাকে হাতে ধরে রাখার শক্তি ছিল না। আমার পিসিমা বলেছিলেন, বাবা নাকি বিয়ের পরেও ঘুড়ি ওড়াতেন, নিজ হাতেই সুতায় মাঞ্জা দিতেন, রঙবেরঙের ঘুড়ি বানাতেন। আমাদের সেই পুরনো ঘরের দেয়াল জুড়ে বাবার আঁকা চিত্রকর্ম ছিল। ঘরের বাইরের দেয়ালে পাকিস্তানী বিখ্যাত চিত্রনায়িকা নিলুর (জন্ম ১৯৪০) বাবার আঁকা প্রতিকৃতি ছিল।
বাবা লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত হয়ে ১৯৭৮ সালের ১৯ জুলাই না ফেরার দেশে চলে যান। তিনজন নাবালক সন্তান নিয়ে আমার মায়ের বেঁচে থাকার জীবন সংগ্রাম দেখেছি। লোকমুখে বাবার কর্মগুণের গল্প শুনে শুনে বড় হয়েছি। বাবা অর্থ-প্রতিপত্তি-যশ-খ্যাতি কোনটা চাননি। চেয়েছিলেন নিজের শিল্পীসত্ত্বার প্রকাশ ঘটাতে ও মানুষের জন্য কিছু করতে। এমন একটি সময় ছিল যখন বরিশাল শহরে বাবার খোঁজে কেউ এলে বাসার ঠিকানা বলার প্রয়োজন হত না, চিত্ত আর্টিস্টের বাসায় যাবো বললে যে কোন রিক্সাওয়ালা বাসায় পৌঁছে দিয়ে যেত। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তিনি তার মৃত্যুর পর রাষ্ট্রীয় গার্ড অব অনার পাননি। মুক্তিবার্তায় তার নম্বর ০৬০১০১০৭৬৬।
বাবার মৃত্যুর পরে সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর থেকে জানতে পেরেছি, বাবাকে সোনারগাঁ’য়ে একটি প্লট সরকার থেকে দেয়ার কথা হয়েছিল, অজ্ঞাত কারণে তিনি তা পাননি। ব্যক্তিগতভাবে তার কবর বাঁধিয়ে দেয়ার কথাও কেউ কেউ বলেছিলেন। তার কবর আজও তেমন থেকে গেছে। কবি সুনীল গঙ্গোপ্যাধায়ের একটি লাইন মনে পড়ছে:‘কেউ কথা রাখেনি, কেউ কথা রাখে না।‘ আমরা একজন আজন্ম শিল্পী ও মুক্তিযোদ্ধার পরিবার বঞ্চিতই থেকে গেছি। আমার মা-ও ভাস্কর্যশিল্পী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার মা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ভাত রান্না করে দিতেন, অনেক মুক্তিযোদ্ধা আমাদের বাসা থেকে খাবার নিয়ে যেতেন। আমার বাবার মৃত্যুর পরে এমনকি তারাও একটু সহানুভূতি জানাতে তেমন কেউ আসেননি। কত সরকার এল—আর গেল। আমাদের কথা কেউ মনে রাখেনি। তার মৃত্যুর পর পর কিছুদিন কেউ কেউ যৎসামান্য খোঁজ নিলেও শিল্পী চিত্ত হালদারের সহযোদ্ধা-বন্ধু-আত্মীয় আমাদের আর খবর নেননি। আমরাও বেঁচে থাকতে জীবনযুদ্ধে সামিল হয়ে গেছি, ছুটতে ছুটতে শুরু করে আর বাবার কাজের দিকে দৃষ্টি দিতে পারিনি। সংরক্ষণের অভাবে তার অনেক কাজ আজ কালের অন্তরালে হারিয়ে গেছে। এ দোষ শুধু আমাদের নয়। আমরা অবহেলিত হয়ে বড় হয়েও বেঁচে থাকার লড়াইয়ে হেরে যাইনি। শুধুমাত্র দুঃখ এটাই যে আমার বাবা ও মা তাদের অবদানের যথাযোগ্য স্বীকৃতি ও মর্যাদা পাননি।